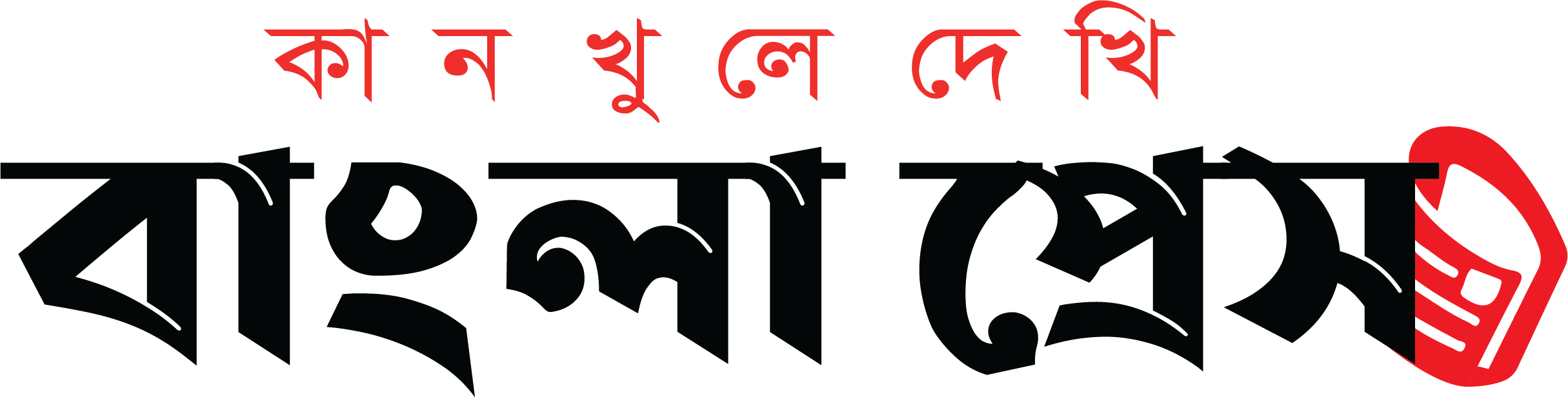ঘড়ি বন্ধক রেখে খাবার খেতেন হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক এলিস
বাংলা প্রেস
প্রকাশ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৭ পিএম

 সাবেদ সাথী: হাতের ঘড়ি বন্ধক রেখে নিয়মিত রেস্তোরাঁয় খাবার কিনে খেতে হতো হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক এলিস আলিসন ডানিগানকে। চল্লিশের দশকে আফ্রিকান-আমেরিকান নারী সাংবাদিকের ভাগ্যে ঘটেছিল এমন অবস্থা।
কেন্টাকিতে জন্ম নেওয়া এ সাংবাদিকই প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান নারী হিসেবে হোয়াইট হাউসের পাশাপাশি মার্কিন কংগ্রেস, সুপ্রিম কোর্ট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কভার করার সুযোগ পেয়েছিলেন।
ওয়াশিংটনে পেশাদারি জীবনের চূড়ায় থাকা অবস্থাতেও খাবার কিনতে এলিস ডানিগানকে প্রতি শনিবার রাতেই ঘড়ি বন্ধক রাখতে হত, সোমবার সকালে বেতনের চেক আসার আগ পর্যন্ত ওই অর্থই ছিল তার সম্বল।
“এটা ছিল অপমানজনক অনুশীলন। কখনোই ৫ ডলারের বেশি পেতাম না,কেবল রোববারের রাতের খাবার পর্যন্তই চলত,” ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী ‘এ ব্ল্যাক ওমেন’স এক্সপেরিয়েন্স- ফ্রম স্কুলহাউস টু হোয়াইট হাউসে’ এমনটাই লিখেছিলেন এ নারী সাংবাদিক।
টাকা নিয়েই ছুটতেন ওয়াশিংটনের ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার ব্রুকল্যান্ড এলাকার এক কামরার বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টে, ভাড়ার টাকা বাঁচাতে যেখানে তাকে ফার্নেসের কয়লা ভাঙতে হত।
১৯৪৭ সালের পর থেকে টানা ১৪ বছর অ্যাসোসিয়েটেড নিগ্রো প্রেসের ওয়াশিংটন ব্যুরো প্রধান ছিলেন এলিস ডানিগান।
“কৃষ্ণাঙ্গ পাঠকদের জন্য অ্যাসোসিয়েটেড নিগ্রো প্রেস ছিল সিএনএন, এমএসএনবিসি ও ওয়াশিংটন পোস্টের যৌথ সংমিশ্রণ। এটি বিক্ষোভের জন্ম দিত, কৃষ্ণাঙ্গদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রতিবাদ জানানো সংগঠনগুলোকে দিত উদ্দীপনা,” বলেন বর্ণবাদের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার জন্য খ্যাত হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গেরাল্ড হর্নে।
১৯৪০ এর মধ্যেই ওই ‘ব্ল্যাক প্রেস’-এর পাঠক প্রায় ১৩ লাখে পৌঁছে গিয়েছিল বলেও এক বইতে জানান এ ইতিহাসবিদ।
“১৯৪০ ও ১৯৫০ এর দশকে সাদাদের কোনো গণমাধ্যমই কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর ছাপত না। এলিস তিনটি প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তিনি যা বলতেন অনেকসময়ই তারা (প্রেসিডেন্ট) তা পছন্দ করতেন না,” বলেছেন ডানিগানের আত্মজীবনীর সম্পাদনাকারী ক্যারল ম্যাককেব বুকার।
২০১৫ সালে বুকার ‘এ ব্ল্যাক ওমেন’স এক্সপেরিয়েন্স- ফ্রম স্কুলহাউস টু হোয়াইট হাউস’ বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন। হোয়াইট হাউসের প্রতিবেদক হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যানের সঙ্গে ওয়েস্ট কোস্ট সফরে যাওয়ার সুযোগ হয় এলিস ডানিগানের। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেতে তখন ‘এখনকার হিসেবে এক থেকে ১০ হাজার ডলারের মত’ খরচ হত; অ্যাসোসিয়েটেড নিগ্রো প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ক্লড বার্নেটকে ওই অর্থ দিতে পারবেন কিনা জানতে চাইলে, ডানিগানের প্রতি ক্লডের জবাব ছিল, “নারীরা এ ধরনের সফরে যায় না।”
ডানিগান নিজস্ব উপায়েই ওই অর্থ জোগাড় করেছিলেন, ফিরেই লিখেছিলেন সাড়াজাগানো প্রতিবেদন, যার শিরোনাম ছিল- ‘মধ্যরাতে পাজামা পরা প্রেসিডেন্ট মুখোমুখি হলেন নাগরিক অধিকারের’।
মন্টানার মিসৌলায় প্রেসিডেন্টের জন্য রেলস্টেশনে অপেক্ষারত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে ঢিলেঢালা গাউন পরেই প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলেন ট্রুম্যান; সেখানেই এক ছাত্র ‘প্রেসিডেন্ট, নাগরিক অধিকার সম্পর্কে আপনার মতামত কি’ জানতে চেয়েছিলেন; তা নিয়েই ছিল ডানিগানের ওই প্রতিবেদন।
১৯৪৮ সালে প্রেসিডেন্টের অভিষেকে কৃষ্ণাঙ্গদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ওয়াশিংটনে ‘সেগরেগেশন আইন’ (শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গেদের পৃথক রাখার আইন) নিষিদ্ধের জন্যও ট্রুম্যানকে বলেছিলেন ডানিগান। সেগরেগেশন আইন নিষিদ্ধ করলে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য হোটেল ও রেস্তোরাঁর বিধিনিষেধ উঠে যেত, এর ফলে তাদের অংশগ্রহণ সহজ হত, যুক্তি ছিল এ নারী সাংবাদিকের।
ট্রম্যান তার ওই প্রস্তাবে সাড়া না দিলেও ‘এটি শান্ত সমুদ্রে বড় একটি পাথর ছুঁড়ে দিয়েছিল, যার ফল মিলেছিল কয়েক বছর পর’, আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেছিলেন ডানিগান।
নাগরিক অধিকার বিষয়ক প্রশ্ন এড়াতে ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর দুই বছর পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলনগুলোতে ডানিগানকে কথা বলার সুযোগ দিতেন না; এরপরও নিরুৎসাহিত করা যেত না এ আফ্রিকান-আমেরিকান নারীকে, ‘মিস্টার প্রেসিডেন্ট, মিস্টার প্রেসিডেন্ট’ বলে ঠিকই নজর কাড়ার চেষ্টা করতেন তিনি, যদিও সাড়া মিলত না।
“তিনি ছিলের বরফের মত শক্ত; হাল ছাড়তেন না, এবং প্রতিটি সংবাদ সম্মেলনেই যেতেন,” বলেন ডানিগানের আত্মজীবনীর সম্পাদনাকারী বুকার। জন এফ কেনেডি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর ডানিগানের এ ‘সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট’ শেষ হয়।
১৯৬১ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম সংবাদ সম্মেলনের ৮ মিনিটের মাথায় এ আফ্রিকান-আমেরিকানকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন কেনেডি। ডানিগান প্রেসিডেন্টের কাছে টেনেসির ফেয়েতে এলাকায় শ্বেতাঙ্গ জমিদারদের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের উচ্ছেদ নিয়ে যে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা থামাতে মার্কিন প্রশাসন কি করছে তা জানতে চান। এ নিয়ে করা এক মামলায় কৃষ্ণাঙ্গরা জয়ী হলে ফেয়েতেতে উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়েছিল।
“কংগ্রেসে এ সংক্রান্ত যে আইন আছে, তাতে সুস্পষ্টভাবে নির্বাহী বিভাগকে মানুষের ভোটের অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি ওই আইনকে সমর্থন করেছিলাম। নাগরিক হিসেবে তার অধিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই প্রত্যেক মার্কিনি যেন ভোট দিতে পারে সে অধিকার নিশ্চিতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলাম আমি; সেকারণেই আমি বলতে পারি, এ সমস্যাটির বেলায়ও প্রশাসন সর্ব শক্তি দিয়েই সে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে,” উত্তরে বলেছিলেন কেনেডি।
১৯০৬ সালে কেন্টাকির রাসেলভিলে জন্ম নিয়েছিলেন ডানিঙ্গান। তার দুই বছর পরই ওই শহরে চার কৃষ্ণাঙ্গকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।
দশকের পর দশক ধরে ছোট ওই শহর এই আতঙ্কের কথা ভুলতে পারেনি। ডানিঙ্গান নিজেও বড় হয়েছেন সেই আতঙ্কের চিত্র মাথায় নিয়েও, যদিও অন্যদের মত আত্মসমর্পণ করে নয়, তিনি লড়েছিলেন।
ইতিহাসবিদ মাইকেল মরো বলছেন, ওয়াশিংটনের মানুষ তাকে গ্রহণ করতে না পারলেও ১৯৮৩ সালে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্তও ডানিগান বুঝতেন, তিনি সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যই ‘এ যুদ্ধে লড়ছেন’।
যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে যারা নাগরিক অধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডানিগানকে তাদের কাতারে নিয়ে আসতে মরো তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছেন; তার এ কষ্ট অবশেষে সফলতার মুখ দেখতে যাচ্ছে।
খবরের জাদুঘর হিসেবে পরিচিত ওয়াশিংটনের নিউজিয়ামে চলতি মাসের ২১ তারিখ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখা মিলবে হোয়াইট হাউসের প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান নারী প্রতিবেদকের একটি ব্রোঞ্জের মূর্তির। ৬ ফুট লম্বা, ৫০০ পাউন্ড ওজনের মূর্তিটি বানিয়েছেন কেন্টাকির ভাস্কর আমান্ডা ম্যাথুজ; যেখানে ডানিগান দাঁড়িয়ে আছেন যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ভালো পোশাক ছিল তার একটি পরে, পায়ে সস্তা জুতা। মূর্তিতে এ আফ্রিকান-আমেরিকান নারীরে হাতে দেখানো হয়েছে ১৯৪৭ সালের ওয়াশিংটন পোস্টের একটি কপি, যার শিরোনামগুলো ঠাসা নাগরিক অধিকারের বিভিন্ন বিষয়ে।
১৯৪৭ সালে ক্যাপিটলের সিঁডিতে দাঁড়ানো অবস্থায় ডানিঙ্গানের একটি ছবির আলোকে ম্যাথুজ এ মূর্তিটি বানিয়েছেন।
সাবেদ সাথী: হাতের ঘড়ি বন্ধক রেখে নিয়মিত রেস্তোরাঁয় খাবার কিনে খেতে হতো হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক এলিস আলিসন ডানিগানকে। চল্লিশের দশকে আফ্রিকান-আমেরিকান নারী সাংবাদিকের ভাগ্যে ঘটেছিল এমন অবস্থা।
কেন্টাকিতে জন্ম নেওয়া এ সাংবাদিকই প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান নারী হিসেবে হোয়াইট হাউসের পাশাপাশি মার্কিন কংগ্রেস, সুপ্রিম কোর্ট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কভার করার সুযোগ পেয়েছিলেন।
ওয়াশিংটনে পেশাদারি জীবনের চূড়ায় থাকা অবস্থাতেও খাবার কিনতে এলিস ডানিগানকে প্রতি শনিবার রাতেই ঘড়ি বন্ধক রাখতে হত, সোমবার সকালে বেতনের চেক আসার আগ পর্যন্ত ওই অর্থই ছিল তার সম্বল।
“এটা ছিল অপমানজনক অনুশীলন। কখনোই ৫ ডলারের বেশি পেতাম না,কেবল রোববারের রাতের খাবার পর্যন্তই চলত,” ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী ‘এ ব্ল্যাক ওমেন’স এক্সপেরিয়েন্স- ফ্রম স্কুলহাউস টু হোয়াইট হাউসে’ এমনটাই লিখেছিলেন এ নারী সাংবাদিক।
টাকা নিয়েই ছুটতেন ওয়াশিংটনের ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার ব্রুকল্যান্ড এলাকার এক কামরার বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টে, ভাড়ার টাকা বাঁচাতে যেখানে তাকে ফার্নেসের কয়লা ভাঙতে হত।
১৯৪৭ সালের পর থেকে টানা ১৪ বছর অ্যাসোসিয়েটেড নিগ্রো প্রেসের ওয়াশিংটন ব্যুরো প্রধান ছিলেন এলিস ডানিগান।
“কৃষ্ণাঙ্গ পাঠকদের জন্য অ্যাসোসিয়েটেড নিগ্রো প্রেস ছিল সিএনএন, এমএসএনবিসি ও ওয়াশিংটন পোস্টের যৌথ সংমিশ্রণ। এটি বিক্ষোভের জন্ম দিত, কৃষ্ণাঙ্গদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রতিবাদ জানানো সংগঠনগুলোকে দিত উদ্দীপনা,” বলেন বর্ণবাদের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার জন্য খ্যাত হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গেরাল্ড হর্নে।
১৯৪০ এর মধ্যেই ওই ‘ব্ল্যাক প্রেস’-এর পাঠক প্রায় ১৩ লাখে পৌঁছে গিয়েছিল বলেও এক বইতে জানান এ ইতিহাসবিদ।
“১৯৪০ ও ১৯৫০ এর দশকে সাদাদের কোনো গণমাধ্যমই কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর ছাপত না। এলিস তিনটি প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তিনি যা বলতেন অনেকসময়ই তারা (প্রেসিডেন্ট) তা পছন্দ করতেন না,” বলেছেন ডানিগানের আত্মজীবনীর সম্পাদনাকারী ক্যারল ম্যাককেব বুকার।
২০১৫ সালে বুকার ‘এ ব্ল্যাক ওমেন’স এক্সপেরিয়েন্স- ফ্রম স্কুলহাউস টু হোয়াইট হাউস’ বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন। হোয়াইট হাউসের প্রতিবেদক হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যানের সঙ্গে ওয়েস্ট কোস্ট সফরে যাওয়ার সুযোগ হয় এলিস ডানিগানের। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেতে তখন ‘এখনকার হিসেবে এক থেকে ১০ হাজার ডলারের মত’ খরচ হত; অ্যাসোসিয়েটেড নিগ্রো প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ক্লড বার্নেটকে ওই অর্থ দিতে পারবেন কিনা জানতে চাইলে, ডানিগানের প্রতি ক্লডের জবাব ছিল, “নারীরা এ ধরনের সফরে যায় না।”
ডানিগান নিজস্ব উপায়েই ওই অর্থ জোগাড় করেছিলেন, ফিরেই লিখেছিলেন সাড়াজাগানো প্রতিবেদন, যার শিরোনাম ছিল- ‘মধ্যরাতে পাজামা পরা প্রেসিডেন্ট মুখোমুখি হলেন নাগরিক অধিকারের’।
মন্টানার মিসৌলায় প্রেসিডেন্টের জন্য রেলস্টেশনে অপেক্ষারত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে ঢিলেঢালা গাউন পরেই প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলেন ট্রুম্যান; সেখানেই এক ছাত্র ‘প্রেসিডেন্ট, নাগরিক অধিকার সম্পর্কে আপনার মতামত কি’ জানতে চেয়েছিলেন; তা নিয়েই ছিল ডানিগানের ওই প্রতিবেদন।
১৯৪৮ সালে প্রেসিডেন্টের অভিষেকে কৃষ্ণাঙ্গদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ওয়াশিংটনে ‘সেগরেগেশন আইন’ (শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গেদের পৃথক রাখার আইন) নিষিদ্ধের জন্যও ট্রুম্যানকে বলেছিলেন ডানিগান। সেগরেগেশন আইন নিষিদ্ধ করলে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য হোটেল ও রেস্তোরাঁর বিধিনিষেধ উঠে যেত, এর ফলে তাদের অংশগ্রহণ সহজ হত, যুক্তি ছিল এ নারী সাংবাদিকের।
ট্রম্যান তার ওই প্রস্তাবে সাড়া না দিলেও ‘এটি শান্ত সমুদ্রে বড় একটি পাথর ছুঁড়ে দিয়েছিল, যার ফল মিলেছিল কয়েক বছর পর’, আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেছিলেন ডানিগান।
নাগরিক অধিকার বিষয়ক প্রশ্ন এড়াতে ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর দুই বছর পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলনগুলোতে ডানিগানকে কথা বলার সুযোগ দিতেন না; এরপরও নিরুৎসাহিত করা যেত না এ আফ্রিকান-আমেরিকান নারীকে, ‘মিস্টার প্রেসিডেন্ট, মিস্টার প্রেসিডেন্ট’ বলে ঠিকই নজর কাড়ার চেষ্টা করতেন তিনি, যদিও সাড়া মিলত না।
“তিনি ছিলের বরফের মত শক্ত; হাল ছাড়তেন না, এবং প্রতিটি সংবাদ সম্মেলনেই যেতেন,” বলেন ডানিগানের আত্মজীবনীর সম্পাদনাকারী বুকার। জন এফ কেনেডি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর ডানিগানের এ ‘সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট’ শেষ হয়।
১৯৬১ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম সংবাদ সম্মেলনের ৮ মিনিটের মাথায় এ আফ্রিকান-আমেরিকানকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন কেনেডি। ডানিগান প্রেসিডেন্টের কাছে টেনেসির ফেয়েতে এলাকায় শ্বেতাঙ্গ জমিদারদের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের উচ্ছেদ নিয়ে যে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা থামাতে মার্কিন প্রশাসন কি করছে তা জানতে চান। এ নিয়ে করা এক মামলায় কৃষ্ণাঙ্গরা জয়ী হলে ফেয়েতেতে উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়েছিল।
“কংগ্রেসে এ সংক্রান্ত যে আইন আছে, তাতে সুস্পষ্টভাবে নির্বাহী বিভাগকে মানুষের ভোটের অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি ওই আইনকে সমর্থন করেছিলাম। নাগরিক হিসেবে তার অধিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই প্রত্যেক মার্কিনি যেন ভোট দিতে পারে সে অধিকার নিশ্চিতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলাম আমি; সেকারণেই আমি বলতে পারি, এ সমস্যাটির বেলায়ও প্রশাসন সর্ব শক্তি দিয়েই সে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে,” উত্তরে বলেছিলেন কেনেডি।
১৯০৬ সালে কেন্টাকির রাসেলভিলে জন্ম নিয়েছিলেন ডানিঙ্গান। তার দুই বছর পরই ওই শহরে চার কৃষ্ণাঙ্গকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।
দশকের পর দশক ধরে ছোট ওই শহর এই আতঙ্কের কথা ভুলতে পারেনি। ডানিঙ্গান নিজেও বড় হয়েছেন সেই আতঙ্কের চিত্র মাথায় নিয়েও, যদিও অন্যদের মত আত্মসমর্পণ করে নয়, তিনি লড়েছিলেন।
ইতিহাসবিদ মাইকেল মরো বলছেন, ওয়াশিংটনের মানুষ তাকে গ্রহণ করতে না পারলেও ১৯৮৩ সালে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্তও ডানিগান বুঝতেন, তিনি সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যই ‘এ যুদ্ধে লড়ছেন’।
যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে যারা নাগরিক অধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডানিগানকে তাদের কাতারে নিয়ে আসতে মরো তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছেন; তার এ কষ্ট অবশেষে সফলতার মুখ দেখতে যাচ্ছে।
খবরের জাদুঘর হিসেবে পরিচিত ওয়াশিংটনের নিউজিয়ামে চলতি মাসের ২১ তারিখ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখা মিলবে হোয়াইট হাউসের প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান নারী প্রতিবেদকের একটি ব্রোঞ্জের মূর্তির। ৬ ফুট লম্বা, ৫০০ পাউন্ড ওজনের মূর্তিটি বানিয়েছেন কেন্টাকির ভাস্কর আমান্ডা ম্যাথুজ; যেখানে ডানিগান দাঁড়িয়ে আছেন যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ভালো পোশাক ছিল তার একটি পরে, পায়ে সস্তা জুতা। মূর্তিতে এ আফ্রিকান-আমেরিকান নারীরে হাতে দেখানো হয়েছে ১৯৪৭ সালের ওয়াশিংটন পোস্টের একটি কপি, যার শিরোনামগুলো ঠাসা নাগরিক অধিকারের বিভিন্ন বিষয়ে।
১৯৪৭ সালে ক্যাপিটলের সিঁডিতে দাঁড়ানো অবস্থায় ডানিঙ্গানের একটি ছবির আলোকে ম্যাথুজ এ মূর্তিটি বানিয়েছেন।
[বাংলা প্রেস হলো মুক্ত চিন্তার একটি বৈশ্বিক প্রচার মাধ্যম। এটি স্বাধীনচেতা মানুষের জন্য নিরপেক্ষ সংবাদ, বিশ্লেষণ ও মন্তব্য সরবরাহ করে। আমাদের লক্ষ্য হলো ইতিবাচক পরিবর্তন আনা, যা আজকের দিনে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।]
আপনি এগুলোও পছন্দ করতে পারেন