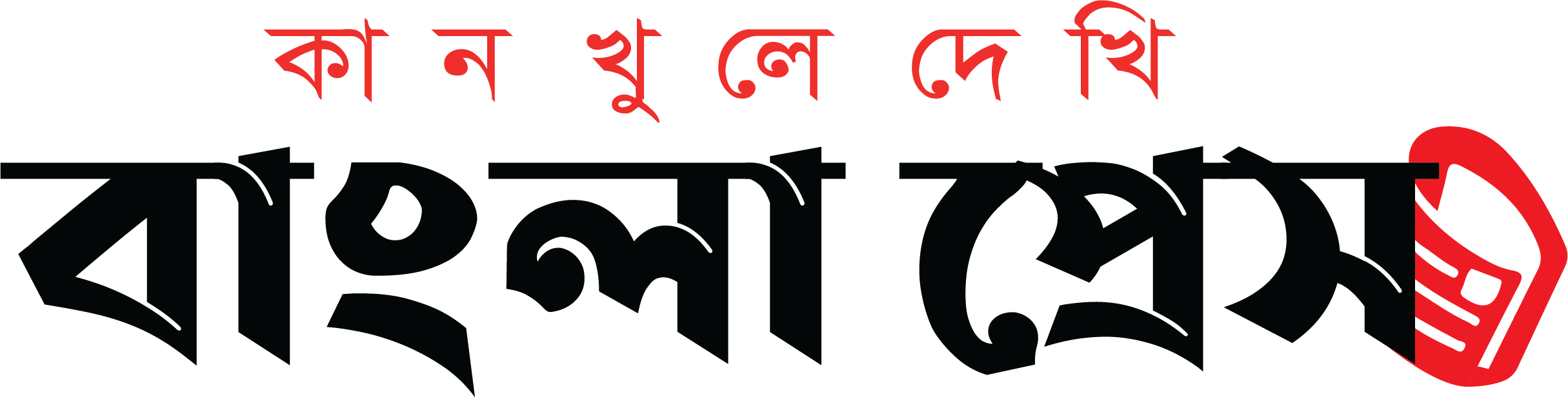এলন মাস্কের ‘আমেরিকা পার্টি’র পেছনের আসল বার্তা

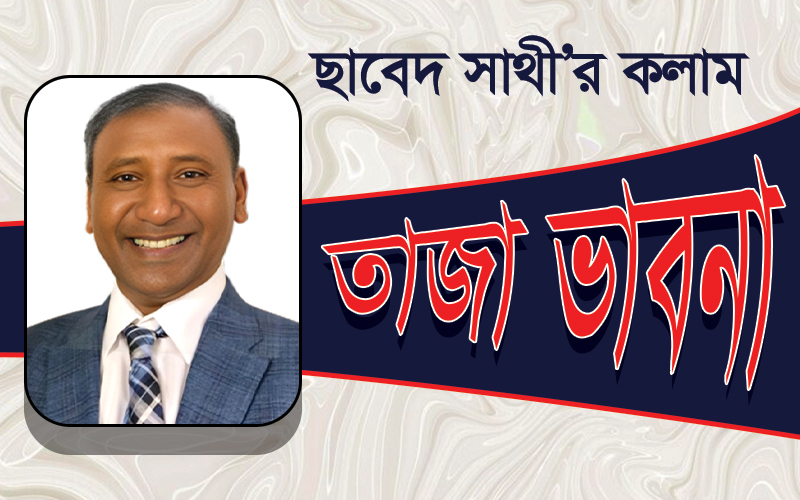
ছাবেদ সাথী
আমেরিকার রাজনীতিতে দেখনদার মানুষের কখনোই অভাব ছিল না। তাই যখন এলন মাস্ক যিনি মহাকাশযান ছোড়ার মতোই সাবলীলভাবে টুইট ছুড়তে পারেন ঘোষণা দিলেন যে তিনি নতুন একটি রাজনৈতিক দল গড়ছেন, তখন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই ছিল সংশয় কিংবা উপহাস। তিনি এটিকে বলছেন 'আমেরিকা পার্টি'একটি পতাকা, যাদের জন্য যারা আর হাতি বা গাধা চায় না (রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রতীক)। স্বভাবতই মিম তৈরি হতে সময় লাগেনি।
কিন্তু এই থিয়েটারের আড়ালে লুকিয়ে আছে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু: তা হলো মানুষের গভীর আকাঙ্ক্ষা। মাস্কের প্রতি জনতার ঢল নাও নামতে পারে, কিন্তু কোটি আমেরিকান নতুন কিছু খুঁজছে। শোটা মাস্কের হতে পারে, কিন্তু তার যে অসন্তোষকে খাওয়াচ্ছে তা বহু মানুষের।
এই মুহূর্তটিকে অতীতের পুনরাবৃত্তি ভেবে উড়িয়ে দেওয়া সহজ। তৃতীয় পক্ষের চেষ্টাগুলো আমেরিকার রাজনৈতিক কিংবদন্তির অংশ হয়ে আছে। থিওডোর রুজভেল্টের ‘বুল মুজ’ বিদ্রোহ থেকে শুরু করে রস পেরোর তথ্যনির্ভর অভিযান অনেকেই দুই প্রধান পার্টির বাইরে কিছু করতে চেয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যবস্থার কাছে পরাস্ত হয়েছেন।
আমেরিকার বিজয়ী-নেই-তো-সব-কিছু কাঠামো আর শক্তিশালী পার্টি-শৃঙ্খলা ঐ পরিবর্তন প্রতিরোধে অদ্ভুত রকম দক্ষ। কিন্তু আজকের পরিবেশটা আলাদা মনে হচ্ছে নিয়মের কারণে নয়, জনমনের কারণে।
চলুন, ‘বিশ্বাস’ দিয়ে শুরু করি যা একসময় ছিল নাগরিক গুণ, এখন তা মৃত প্রায়। পিউ রিসার্চের এক জরিপ বলছে, মাত্র ২২ শতাংশ আমেরিকান বিশ্বাস করে যে ফেডারেল সরকার 'প্রায় সবসময়' বা 'অধিকাংশ সময়' ঠিক কাজ করে যেখানে ১৯৬০-এর দশকে এই সংখ্যা ছিল ৭০ শতাংশের বেশি। গ্যালাপ বলছে, কংগ্রেসের প্রতি আস্থা ১০ শতাংশের নিচে। এটি উদাসীনতা নয়; এটি হতাশা একটা ব্যাপক বিশ্বাস, যে বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামো আর শোনে না, কাজ তো করেই না।
জুলাই ৩ তারিখে মাস্ক 'আমেরিকা পার্টি' ঘোষণা দেন, যা তাৎক্ষণিকভাবে ২০২৬ সালের প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে জল্পনা তৈরি করে। স্ন্যাপপোল২৪-এর এক জরিপে দেখা গেছে, জেনারেশন জি ও মিলেনিয়ালদের মধ্যে ২৭ শতাংশ “অরাজনৈতিক প্রার্থীকে” সমর্থনে আগ্রহী এক দশক আগেও যা অকল্পনীয় ছিল।

এই শূন্যতার মাঝেই মাস্ক হাজির হয়েছেন। নীতির মাধ্যমে নয়, বরং পারফরম্যান্স দিয়ে। আর এক মিডিয়া বাস্তবতায়, যেখানে মনোযোগই ক্ষমতা, সেটাই অনেক সময় যথেষ্ট। তার দলীয় নীতি এখনও অস্পষ্ট, কিন্তু আবেদন পরিষ্কার: আদর্শ ছাড়া বিদ্রোহ।
এই সময়ে, যেখানে ডেমোক্র্যাটরা অভিজাত প্রগতিবাদের ভাষায় কথা বলে আর রিপাবলিকানরা ঘুরপাক খায় অভিমান ও লোকরঞ্জনবাদে সেখানে মাস্ক এক তৃতীয় পথ দেখাচ্ছেন, যা সংজ্ঞায়িত হয় বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে, আদর্শ দিয়ে নয়।
নির্বাচনে নামার পথে বাধা অবশ্য এখনো বিশাল। ব্যালট-প্রবেশের কঠিন আইন, অর্থায়নের সীমা, এবং পার্টি-নিষ্ঠার কায়েমি শক্তি সবই একসাথে কাজ করে বহিরাগতদের রুখে দিতে। কিন্তু প্রযুক্তি, যা একসময় ক্ষমতাসীনদের অস্ত্র ছিল, এখন সেই ব্যবধান ঘোচাচ্ছে। এক স্মার্টফোন, প্রচুর অর্থ আর অনুগত অনলাইন অনুসারী থাকলে, কোনো প্রার্থী গেটকিপারদের পাশ কাটিয়ে সামনে আসতে পারেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬-তে সেটি করেছিলেন। বার্নি স্যান্ডার্সও এক মাইক্রোফোন আর ইমেইল তালিকায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।
আর সত্যি বলতে, এখন কেন্দ্র ধরে রাখা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক মেরুকরণ পার্টিগুলোকে দুই চরমে ঠেলে দিয়েছে, মাঝখানে তৈরি হয়েছে বিশাল এক শূন্যতা যেখানে স্বাধীন, মধ্যপন্থী আর শহরতলির ভোটাররা ছড়িয়ে আছে কোনো পক্ষ না নিয়ে। সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, ৪৩ শতাংশ আমেরিকান নিজেদের স্বাধীন ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করে। নতুন কণ্ঠের প্রতি আগ্রহ বাস্তব। প্রশ্ন হলো, সেটা কি সংগঠিত কোনো রাজনৈতিক শক্তিতে রূপ নিতে পারবে?
সেখানেই বেশিরভাগ তৃতীয় পক্ষ ব্যর্থ হয়। তারা অসন্তোষ প্রকাশে পারদর্শী, কিন্তু শাসনের ক্ষেত্রে নীরব। তারা রাগ নিয়ে এগোয়, কিন্তু সমাধানে থেমে যায়। এটা শুধু দুর্বলতা নয়, কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা। পপুলিজম, ডান বা বাম বিক্রি করা সবচেয়ে সহজ যখন লক্ষ্য কেবল বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বিদ্রুপ করা। কিন্তু শাসন মানে আপস, যা মাস্ক বরাবরই অবহেলা করেছেন চাই সেটা টানেল বানানো হোক কিংবা নীতিগত টুইট দেওয়া।
তবু, বিপর্যয়ও মূল্যবান, এমনকি ব্যর্থ হলেও স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে, এটা কখনো কখনো পুরনো দলগুলোকে সাড়া দিতে বাধ্য করে। ফ্রান্সে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর কথা ভাবুন। তার উদীয়মান দল এক পচে যাওয়া ব্যবস্থাকে উলটে দিয়েছিল, নিখুঁত ছিল না, কিন্তু নতুন ছিল বলে মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছিল। ইতালি, চিলি, তাইওয়ানেও এমন ঘটেছে যেখানে পুরনো দলগুলো নিজেদের অলসতায় ধসে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আরও পুরনো আর শক্ত কাঠামোর, কিন্তু চাপ এখানে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা কোনো স্থায়ী রাজনৈতিক দল কল্পনা করেননি। তারা বানিয়েছিলেন একটি কাঠামো যেখানে ভারসাম্য, ফেডারালিজম, এবং একে অপরকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে যা কোনো দল টিকবে কি না, তার চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী। এই স্থিতিশীলতাই এক অর্থে সমস্যা: এটা একদিকে স্বৈরতন্ত্র ঠেকায়, অন্যদিকে স্থবিরতাও বাঁচিয়ে রাখে। পরিবর্তন, যখন আসে, হয়তো পরিপাটি হয় না, কিন্তু প্রায়ই আসে সেসব লোকদের হাত ধরে যাদের কাছ থেকে সেটা কেউ আশা করে না।
তাই না, ‘আমেরিকা পার্টি’ সম্ভবত কংগ্রেস দখল করতে পারবে না। হয়তো এটি এক নিউজ সাইকেলও টিকবে না। কিন্তু এর আবির্ভাব একটি সংকেত যে ব্যবস্থার ভিতরেই অস্থিরতা জমে উঠছে। ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকানরা যদি এটিকে উপেক্ষা করে, তাহলে সেটা তাদের নিজেদের ঝুঁকি। ভোটাররা নির্লিপ্ত নয় তারা হতাশ। আর যদি মাস্কের এই প্ররোচনা পার্টিগুলোকে বাধ্য করে বিশ্বাস অর্জনের উপায় নতুনভাবে ভাবতে, তাহলে তার এই ‘পাগলামিও’ উদ্দেশ্য সফল বলে বিবেচিত হবে।
এই নতুন কণ্ঠগুলোকে দমন নয়, বরং তাদের সমালোচনা শুনে ব্যবস্থা নেওয়াই হবে আমেরিকার রাজনৈতিক কাঠামোর চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা। র্যাংকড-চয়েস ভোটিং, উন্মুক্ত প্রাইমারি আর ক্যাম্পেইন অর্থায়ন সংস্কার কোনো ম্যাজিক নয়, কিন্তু হয়তো এটাই সেই ভিত্তি যা এক শ্রুতিশীল গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন যা ধ্বংসের আগেই শুনতে শেখে।
প্রায়ই বলা হয়, গণতন্ত্র নিজেদের নতুন করে গড়ে তোলে বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, বরং অভিযোজনের মাধ্যমে। সম্ভবত এখন সেই সময়। আর হয়তো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, দুই প্রধান পার্টিকে টুইটবোমা ছুড়ে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, গণতান্ত্রিক ভারসাম্য কোনো স্থির বস্তু নয়। এটা স্থান বদলায় কখনো হঠাৎ, আর প্রায়শই তাদের পায়ের নিচ দিয়ে।
ছাবেদ সাথী: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী লেখক, সাংবাদিক ও মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সম্পাদক বাংলা প্রেস
[বাংলা প্রেস বিশ্বব্যাপী মুক্তচিন্তার একটি সংবাদমাধ্যম। স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের জন্য নিরপেক্ষ খবর, বিশ্লেষণ এবং মন্তব্য সরবরাহ করে। আমাদের লক্ষ্য হলো ইতিবাচক পরিবর্তন আনা, যা আজ আগের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।] বিপি।সিএসআপনি এগুলোও পছন্দ করতে পারেন