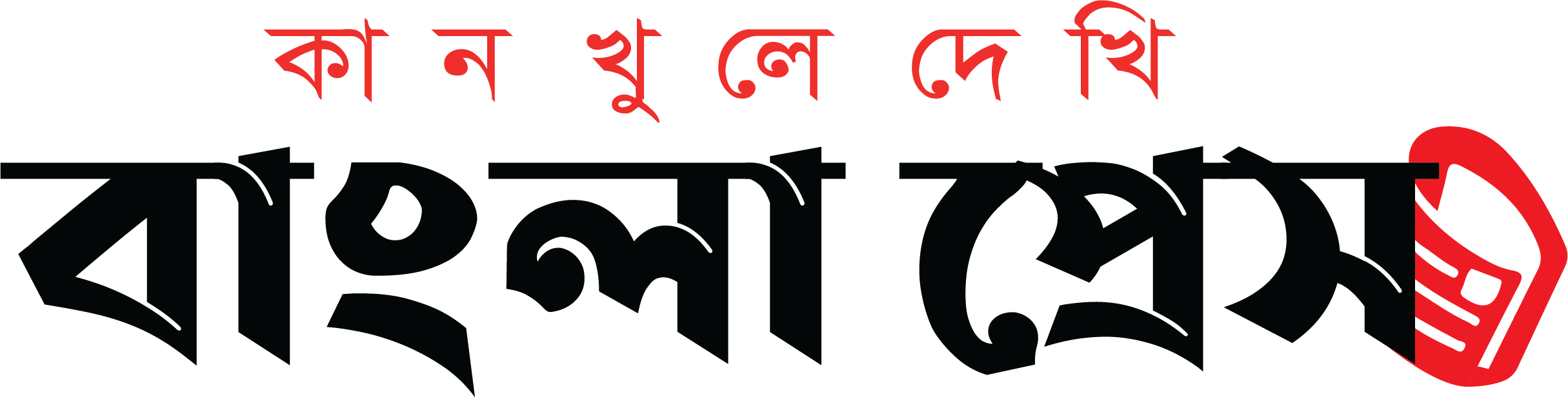ট্রাম্পের শুল্ক চাষ বনাম বৃটিশদের নীল চাষ


ছাবেদ সাথী
বিশ্বের অর্থনীতি আজ আবারও এক নতুন ধরনের ‘বাণিজ্য যুদ্ধ’-এর মুখোমুখি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে বিশ্বব্যাপী আমদানি–রপ্তানি নীতিতে কড়া শুল্ক আরোপের মাধ্যমে এমন এক বাণিজ্য কাঠামো তৈরি করেছেন, যা অনেক বিশ্লেষকের মতে ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার পর সবচেয়ে বড় শুল্কবৃদ্ধির উদাহরণ। জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে নতুন চুক্তি, চীন–কানাডা–মেক্সিকোর সঙ্গে অনিশ্চিত আলোচনা—সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে।
ট্রাম্পের শুল্ক নীতি: স্বদেশি শিল্প বনাম বৈশ্বিক শৃঙ্খলা
ট্রাম্প প্রশাসন ‘পারস্পরিক শুল্কের’ নীতি অনুসরণ করছে—যে দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে যত শুল্ক বসাবে, আমেরিকাও সেই দেশের পণ্যে সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি শুল্ক বসাবে। এতে একদিকে স্বদেশি শিল্প সুরক্ষিত হতে পারে, কিন্তু অন্যদিকে আমদানি–নির্ভর শিল্পখাত চাপে পড়ে এবং ভোক্তাদের ওপরও মূল্যবৃদ্ধির বোঝা পড়ে। জাপানকে ২৫ শতাংশের বদলে ১৫ শতাংশ শুল্কে রাজি করানো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষ চুক্তি—এসবই ট্রাম্পের ‘কঠোর কিন্তু লাভজনক’ বাণিজ্য কৌশলের অংশ। তবে এই কৌশল বিনিয়োগকারীদের কাছে দীর্ঘমেয়াদে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে।
নীলচাষ: ঔপনিবেশিক যুগের শুল্ক–শোষণ
আজ থেকে দেড় শতাব্দী আগে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় বাংলার কৃষকরা এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়েছিলেন নীলচাষের মাধ্যমে। ইংরেজ বণিকেরা চুক্তির নামে কৃষকদের জমিতে জোর করে নীল গাছ লাগাতেন। ধান বা খাদ্যশস্য উৎপাদনের বদলে নীলচাষ করতে বাধ্য হওয়ায় খাদ্যসংকট দেখা দিত। নীল রঙ উৎপাদন ও রপ্তানির মূল লাভ যেত ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পকেটে; কৃষকের হাতে থাকত সামান্য অগ্রিম ও ঋণের বোঝা। ব্রিটিশরা আন্তর্জাতিক বাজারে নীলের দাম নিজেদের সুবিধামতো ঠিক করত, আর ভারতীয় কৃষক ছিল সেই দামের ‘বন্দি’।
১৮৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের দিকে নীল বিদ্রোহের সূচনা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মাটি ছিল নীল চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বিপুল লাভের আশায় ব্রিটিশ নীলকররা নীল চাষের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেন। নদীয়া, রংপুর, যশোর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় নীল চাষ শুরু হয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে এই নীল চাষ আর অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক থাকে না। ফলে চাষীরা নীল চাষ না করে ধান, পাট চাষ করতে চান। কিন্তু নীলকর সাহেবরা চাষীদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার, দমন পীড়ন নামিয়ে তাদেরকে নীল চাষ করতে বাধ্য করে। এর বিরুদ্ধে চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে নীল চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ইতিহাসে এই আন্দোলন 'নীল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।
নীল চাষ যখন প্রথম শুরু হয়েছিল তখন নীল চাষ ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া দখলে। কিন্তু ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের ফলে এই একচেটিয়া অধিকার আর থাকল না, ব্রিটেন থেকে বহু সংখ্যক নীলকর বাংলায় এসে ইচ্ছেমতো নীল চাষ শুরু করে। কৃষকদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার। ১৮৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস নাগাদ নীলচাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে নীল চাষ করবে না বলে ঘোষণা করে। নীল চাষীদের এই আন্দোলন দমন করার জন্য শুরু হয় ভয়ানক পুলিশি অত্যাচার, গ্রেফতার করা হয় আন্দোলনকারীদের। এর উল্টোদিকে নীল চাষীদের আন্দোলনও আরও বৃহৎ আকার ধারণ করে। ইংরেজ সরকার ১৮৬০ সালে 'নীল কমিশন' গঠন করে, নীল বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে। এই কমিশন তদন্ত করে চাষীদের অভিযোগ যথার্থ বলে রায় দিয়েছিল। এরপর সরকার নীল চাষের ওপর আইন পাশ করতে বাধ্য হয় ১৮৬২ সালে।
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে বস্ত্র শিল্পের বিপুল চাহিদা তৈরি হয়, ফলে কাপড় রঙ করার জন্য নীলের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেইসময় নীল চাষ অন্যতম লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। একটি হিসেবে দেখা যায় যে- ১৮০৩ সাল পর্যন্ত নীল চাষ করতে যে খরচ হত, তার সবটাই কোম্পানি অল্প সুদে আগাম দিয়ে দিত। এতে যে নীল উৎপাদিত হত, তার সবটাই চলে যেত ইংল্যাণ্ডে, কোম্পানির লাভের অঙ্ক বেড়ে চলত বহুগুণে। একে একে খুলনা, ২৪ পরগণা, রাজশাহী, মালদা, পাবনা, ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় অসংখ্য নীলকুঠি গড়ে ওঠে। নীল চাষের লাভজনক প্রসার দেখে বাংলার শীর্ষস্থানীয় মুৎসুদ্দি, জমিদার-গোষ্ঠী, প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন শহুরে মানুষেরা নীল চাষের প্রসারের জন্য আন্দোলন করেছিল। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজ সরকারের সুনজরে থাকা। এদের মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ছিলেন। এঁরা ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮২৯ কলকাতার টাউন হলে সভা করে নীল চাষ প্রসারের দাবী জানিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একাধিক কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা চালা
বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার (তৎকালীন নদীয়া) চৌগাছাতে প্রথম নীল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে। এরপর এই বিদ্রোহের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, খুলনা প্রভৃতি জেলায়। কৃষকরা বহু নীলকুঠি ভেঙে দেয়। অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের মাল বহনের যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। নীল বিদ্রোহে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে যোগদান করেছিল। নীল বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এবং জমিদারদের প্রত্যক্ষ মদতে পুলিশ কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালাত। কিন্তু তাতে এই আন্দোলন থেমে যাওয়ার পরিবর্তে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। নদীয়া জেলার দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, পাবনার কাদের মোল্লা, মালদার রফিক মণ্ডল এই আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতৃত্ব ছিলেন। অত্যাচারী নীলকরদের রীতিমতো ভয়ের কারণ ছিলেন আন্দোলনকারী বিশ্বনাথ সর্দার, তাঁর নেতৃত্বে একাধিক নীলকুঠি আক্রমণ করা হয়েছিল। নদীয়ার আসান নগরে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের মতে, বিশ্বনাথ সর্দারকে নীল বিদ্রোহের প্রথম শহীদ হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে, ইংরেজরা না।
ব্রিটিশ শাসকদের ওপর এই নীল বিদ্রোহের প্রভাব ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহের খবর ইংল্যান্ডে পৌঁছানো মাত্রই ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কৃষকদের দুরবস্থার বিষয়ে ইংরেজ শাসকদের কাছে কৈফিয়ত চায়- নীল বিদ্রোহ ও চাষীদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সবকিছু তদন্ত করে নীল গাছের দাম বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে লাভের পরিমাণ কমে আসায় নীলকর সাহেবরা নীল তৈরির কারখানাগুলো বিক্রি করে দেয়। ১৮৯৫ সালে নীলের উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে এই ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় তারা।
১৮৫৯ সালে দীনবন্ধু মিত্র নীল বিদ্রোহ নিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নাটকটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। রেভারেন্ড জেমস লং এই ইংরেজি নাটকটি প্রকাশ করেন। সেই অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাকে কারাদণ্ড ও জরিমানার শাস্তি দিয়েছিল। সাহিত্যক কালীপ্রসন্ন সিংহ তার জরিমানার টাকা পরিশোধ করেছিলেন। নীল বিদ্রোহের সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

অতীত ও বর্তমানের মিল–অমিল
ট্রাম্পের শুল্ক–বাণিজ্য নীতি ও ব্রিটিশদের নীলচাষ দুই প্রেক্ষাপটই আলাদা, তবু একটি মৌলিক সাদৃশ্য আছে: উভয় ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর একপক্ষ বাণিজ্যের শর্ত নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করছে। নীলচাষে যেমন ব্রিটিশরা বিশ্ববাজারে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ভারতীয় কৃষকদের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করত, তেমনি আজ যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যের শর্ত নির্ধারণ করছে। পার্থক্য হলো, নীলচাষ ছিল সরাসরি উপনিবেশিক শোষণ; বর্তমান শুল্ক–নীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কূটনৈতিক খেলার অংশ।
শিক্ষা ও সতর্কবার্তা
ইতিহাস দেখিয়েছে, একপক্ষীয় বাণিজ্যিক আধিপত্য শেষ পর্যন্ত সামাজিক–অর্থনৈতিক ক্ষোভ ও অস্থিরতা ডেকে আনে। ১৮৫৯–৬০ সালের নীলবিদ্রোহ ছিল বাংলার কৃষকের অসহায়ের প্রতিবাদ, যা বিশ্বকে উপনিবেশিক শোষণের ভয়াবহতা দেখিয়েছিল। আজকের শুল্ক–বাণিজ্য যুদ্ধও যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে তা বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে এবং ছোট–বড় দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে।
উপসংহার
ব্রিটিশদের নীলচাষ ও ট্রাম্পের শুল্ক–নীতি—দুই ঘটনাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাণিজ্য কেবল অর্থনীতির প্রশ্ন নয়; এটি ক্ষমতা, রাজনীতি ও মানবিক ন্যায়েরও প্রশ্ন। ইতিহাসের শিক্ষা হলো—যে নীতি একপক্ষীয়ভাবে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা কখনোই দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকে না।
ছাবেদ সাথী: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী লেখক, সাংবাদিক ও মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সম্পাদক বাংলা প্রেস [বাংলা প্রেস বিশ্বব্যাপী মুক্তচিন্তার একটি সংবাদমাধ্যম। স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের জন্য নিরপেক্ষ খবর, বিশ্লেষণ এবং মন্তব্য সরবরাহ করে। আমাদের লক্ষ্য হলো ইতিবাচক পরিবর্তন আনা, যা আজ আগের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।] বিপি। সিএসআপনি এগুলোও পছন্দ করতে পারেন